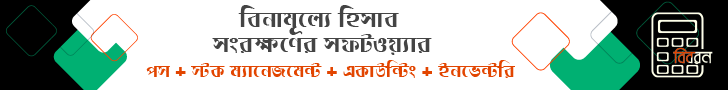ভ্যাট বন্ধু নিউজ প্রতিবেদক
১৮ মে, ২০২৪ | ৯:২৫ এএম
অনলাইন সংস্করণ
নিয়ন্ত্রণে নেই ওষুধের দাম
১৮ মে, ২০২৪ | ৯:২৫ এএম

ঔষধ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে নেই ৯৭ শতাংশ ওষুধের দাম। ফ্রিস্টাইলেই যেন ওষুধ কোম্পানিগুলো ওষুধের দাম বাড়িয়ে চলেছে। দেশে প্রতিদিন হু হু করে বাড়ছে জীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ওষুধের দাম।
পর্যবেক্ষকরা বলছেন, ওষুধের দাম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ওষুধের কাঁচামাল, লেবেল কার্টন, মোড়ক সামগ্রী, মার্কেটিং খরচ ও ডলারের দাম বৃদ্ধিসহ নানা অজুহাতে এবং ওষুধ কোম্পানিগুলো ঔষধ প্রশাসনকে ‘ম্যানেজ’ করে ইচ্ছেমতো ওষুধের মূল্য বছরের পর বছর বাড়িয়ে যাচ্ছে। যার ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতা-উভয়েই তাদের কাছে জিম্মি হয়ে পড়ছে। তাই ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির এ প্রবণতা রুখতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো সব ওষুধকে ফর্মুলার ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞ-পর্যবেক্ষকরা। একই সঙ্গে স্বাধীন কমিশন গঠন করাসহ বেশ কিছু সুপারিশ ও প্রস্তাবনাও দিয়েছেন তারা।
ঔষধ প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে দেশে ৩৫ হাজার ২৯০টি ব্র্যান্ডের ৪১৮০টি অত্যাবশ্যকীয় বা জেনেরিকের (৯৭ দশমিক ২১ শতাংশ) ওষুধ বিভিন্ন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবায় অ্যাসেনসিয়াল ড্রাগ হিসেবে পরিচিত ১১৭টি জেনেরিকের ৪১৭টি (২ দশমিক ৭৯ শতাংশ) মূল্য নির্ধারণ করে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর। অর্থাৎ ৯৭ শতাংশ ওষুধের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা নেই ‘ঠুঁটো জগন্নাথ’ সংস্থাটির। আর এ সুযোগে ইচ্ছেমতো ৪ হাজার ৬৩টি ব্র্যান্ডের ওষুধের দাম নির্ধারণ করে ফার্মাসিটিক্যাল কোম্পানিগুলো।
অথচ ১৯৮২ সালে ওষুধনীতি নিয়ে জারি করা অধ্যাদেশে বলা হয়, ওষুধের মান নিশ্চিত করবে কোম্পানি। নজরদারি ও দাম নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার। তখন ১৫০টি জেনেরিক ওষুধের দাম নির্ধারণ করার ক্ষমতা ছিল সরকারের হাতে। ১৯৯৪ সালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা কমিয়ে ১১৭টি জেনেরিকের ওষুধের দাম নির্ধারণ করা হয়। বাকি ওষুধের দাম নির্ধারণের ক্ষমতা দেওয়া হয় কোম্পানির হাতে।
জানা গেছে, সরকারের ‘প্রাইস ফিক্সেশন পলিসি-১৯৯২’ বা মূল্য নির্ধারণ নীতি অনুযায়ী, দেশে প্রতি বছর অত্যাবশ্যকীয় তালিকাভুক্ত ওষুধের মূল্য সমন্বয় করার কথা রয়েছে। কিন্তু ১৯৯২ সালে ওই নীতিমালা হওয়ার পর তিন দফায় এগুলোর মধ্যে কিছু ওষুধের মূল্য পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল। সবশেষ ২০২২ সালে ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানিগুলো ফের মূল্যবৃদ্ধির জন্য ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরে আবেদন করে। তখন ১৯ জেনেরিকের ৫৩টি ওষুধের সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য বৃদ্ধি করে সরকার।
ওষুধ প্রস্তুতকারি কোম্পানিগুলোর সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, অত্যাবশ্যকীয় তালিকাভুক্ত ওষুধের দাম নির্ধারণের একটি ফর্মুলা বা সূত্র রয়েছে। তা হলো কাঁচামালের দাম, প্যাকিং উপকরণের দাম এবং মার্কআপ যা এমআরপি (ভ্যাট ছাড়া)। আর অত্যাবশ্যকীয় তালিকাভুক্ত যেসব ওষুধের দাম নির্ধারণ করা নেই অথবা কোনো ওষুধের দাম সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আবেদন করতে হয়।
সংশ্লিষ্টরা জানান, দেশে নতুন করে ওষুধ ও কসমেটিকস আইন ২০২৩-এর ৩০(১) (২) ধারা অনুযায়ী শুধু গেজেটে প্রকাশিত তালিকাভুক্ত ওষুধগুলোর খুচরা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সরকার। এ সুযোগে ওষুধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো ইচ্ছেমতো মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ নিচ্ছে। গত কয়েক মাসের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট, ইনসুলিন ও ইনজেকশন, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা, হাঁপানিসহ বিভিন্ন ওষুধ ও ভিটামিনের দামও বেড়েছে। বাদ যায়নি জ্বর-ঠান্ডার ট্যাবলেট-ক্যাপসুলসহ নানা রোগের সিরাপও। এতে জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলো সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্তরাও ওষুধ কিনতে হিমশিম খান।
আর ওষুধের মূল্যবৃদ্ধির জন্য বিশ্ববাজারে ওষুধের কাঁচামাল, মার্কেটিং খরচ, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসসহ ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধিকে দায়ী করছে ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত জেনেরিকসহ বিভিন্ন ওষুধের দাম ৭ থেকে ১৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইচ্ছামতো সব ধরনের ওষুধের মূল্যবৃদ্ধি ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট।
ওষুধের দাম বৃদ্ধির বিষয়ে হাডসন ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাংলাদেশ ওষুধ শিল্প মালিক সমিতির মহাসচিব এসএম শফিউজ্জামান বলেন, বর্তমানে দেশের চাহিদার ৯৮ শতাংশ পূরণ করছে দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানির উৎপাদিত ওষুধ। কিন্তু দেশীয় ওষুধশিল্পের প্রসারে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। কিন্তু দাম বাড়ানোর জন্য আমরা যতই আবেদন করি না কেন ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর যদি অনুমোদন না করে এবং কোনো সিদ্ধান্ত না নেয় তা হলে দাম বাড়ানোর কোনো সুযোগ নেই।
ওষুধের দাম কীভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এ বিষয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়ে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের সাবেক উপ-পরিচালক ড. মো. নূরুল আলম বলেন, গেজেট সংশোধন করে ১১৭টি জেনেরিকের পরিবর্তে মোট ওষুধের এক-তৃতীয়াংশ অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার ওষুধের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর অধিকাংশ ওষুধ উৎপাদনের কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। তাছাড়া লেবেল কার্টন, মোড়কসামগ্রী এবং মার্কেটিং খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। কোম্পানিগুলো গেটআপ আকর্ষণীয় করতে চকচকে মোড়কে ওষুধ বাজারজাত করে থাকে। প্রায় সব বড় কোম্পানি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা এমআরের মাধ্যমে ওষুধ মার্কেটিং করে থাকে। যার সংখ্যা কয়েক লাখ হতে পারে। এ সব জনবলের বেতন-ভাতা, মোটরসাইকেলের জ্বালানি উৎপাদিত ওষুধের মূল্যের সঙ্গে মার্কেটিং খরচ হিসেবে সমন্বয় করা হয়ে থাকে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আবদুল হামিদ বলেন, পৃথিবীজুড়েই ওষুধের দাম নির্ধারণে একটি আলাদা ব্যবস্থাপনা বা অথরিটি আছে। তাতে ওষুধের দাম নির্ধারণে গভর্মেন্টের ভূমিকা থাকে। এমনকি ভারতেও প্রাইস মনিটরিংয়ের জন্য আলাদা সংস্থা রয়েছে। তারা ঠিক করেন কোন ওষুধের দাম কী হবে। কিন্তু আমাদের দেশে ব্যতিক্রম। সবই ঔষধ প্রশাসন করে। ওষুধের দাম বাড়লে সাধারণ মানুষের বিপদ হয়। এমনিতেই সব জিনিসের দাম বাড়তি। ফলে তাদের অনেক কষ্ট হয়। যেমন চাল বা আটার দাম বেড়ে গেলে কম দামি চাল বা আটা খাওয়া যায়, কিন্তু ওষুধের ক্ষেত্রে তো তা না। কারণ ওষুধের তো কোনো বিকল্প নেই।
তিনি বলেন, বাজারে ২০১৫ সালে কিংবা ২০২০ সালে ওষুধের যে দাম ছিল তা এখন আশা করা যায় না। কারণ সবকিছুরই দাম বেড়েছে। তাই বাজারে যেসব ওষুধ বেশি বিক্রি হয় সেগুলোকে ফর্মুলার আওতায় আনা জরুরি। আর ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিগুলো বিদেশ থেকে কাঁচামাল আমদানি করছে। তারা দেখায় এক রকমের দাম, যে তারা জার্মানি কিংবা অন্য দেশ থেকে আনছে এবং খরচ দেখাচ্ছে বেশি। কিন্তু দেখা গেলে কাঁচামাল ভারত অথবা চীন থেকে কম দামে আনা হচ্ছে অথচ ওষুধের দাম নির্ধারণের ভুল তথ্য দেখিয়ে বেশি দাম দেখাচ্ছে।
কিন্তু ওষুধ তৈরি করছে কম দামি কাঁচামাল দিয়ে। এ ক্ষেত্রে ঔষধ প্রশাসনের খতিয়ে দেখা উচিত আসলে কাঁচামাল কোন দামে আনছে এবং তার মূল্য কত-তাই তাদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। আর ওষুধের মালামাল তৈরিতে বিদেশ থেকে যেসব সরঞ্জাম আমদানি করতে হয় তার যদি শুল্ক থাকে তা কমিয়ে দিতে হবে এবং কোম্পানিগুলোর সঙ্গে সরকার একটি শর্তে আসতে পারে, দামের শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে-তাই ওষুধের দাম বাড়বে না। দাম যাতে রেঞ্জের মধ্যে থাকে, সেটি সরকারকে ইনশিউর করতে হবে।
আর ওষুধ বিক্রিতে মার্কেটিং খরচও একটি বড় খরচ, তাই ওষুধ শিল্প সমিতি একটি পদক্ষেপ নিতে পারে-তা হলো ডাক্তারদের কমিশনসহ অন্যান্য খরচ ১০ থেকে ২০ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারে। এতে ওষুধের দাম অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে পারে বলেও মত দেন এই অধ্যাপক।
ড. আবদুল হামিদ বলেন, ওষুধের দাম না বাড়ার কারণে কোম্পানিগুলো জেনেরিক ওষুধের যে ফর্মুলা রয়েছে তা থেকে বেরিয়ে ইচ্ছেমতো দাম নির্ধারণ করে থাকে। যেমন প্যারাসিটামলের সঙ্গে ক্যাফেইন যুক্ত করে নতুন নাম দিল নাপা প্লাস বা নাপা এক্সট্রা। অর্থাৎ তারা ১১৭টি জেনেরিক ওষুধের ফর্মুলা থেকে বেরিয়ে পছন্দমতো দাম নির্ধারণ করছে। বাজারে এভাবেই ফর্মুলার বাইরের ওষুধের দাম বাড়ছে। তাই এই জায়গাটা সরকারকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। তাই দাম নিয়ন্ত্রণের প্রথম উপায় হচ্ছে জেনেরিক ওষুধের দাম নিয়মতান্ত্রিক ও নিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়াতে হবে। আর পর্যায়ক্রমে বাজারে যে সব ওষুধ রয়েছে তা ১১৭টি জেনেরিক ওষুধের সঙ্গে সব ওষুধ যুক্ত করে ফর্মুলার আওতায় নিয়ে আসতে হবে।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ছে কি না। আর নিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়ার জন্য সরকার ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর করেছে। কিন্তু সেটি তার মূল কাজ ওষুধের দাম নির্ধারণ করা না। তার কাজ হলো ওষুধের স্ট্যান্ডার্ড বা কোয়ালিটি ঠিক আছে কি না, তা দেখার। কিন্তু তাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই ঔষধ প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে হবে।
ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের পরিচালক ডা. আশরাফ হোসেন বলেন, ওষুধের দাম নির্ধারণে বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারকরা জড়িত। এটা শুধু একা অধিদফতরের কাজ নয়। ১৯৯৪ সালের গেজেটের পর অনেক অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ বাজারে এসেছে। এই তালিকা বড় করা গেলে তা ওষুধের মূল্য বহুলাংশে কমাতে সহায়ক হবে।
- ট্যাগ সমূহঃ
- ওষুধ
 ভ্যাট বন্ধু নিউজ-এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন
ভ্যাট বন্ধু নিউজ-এর সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন